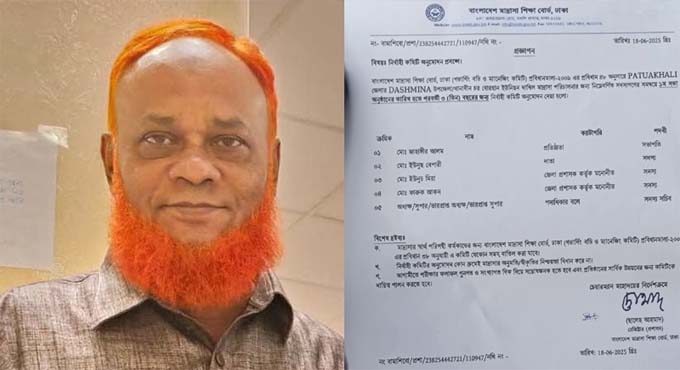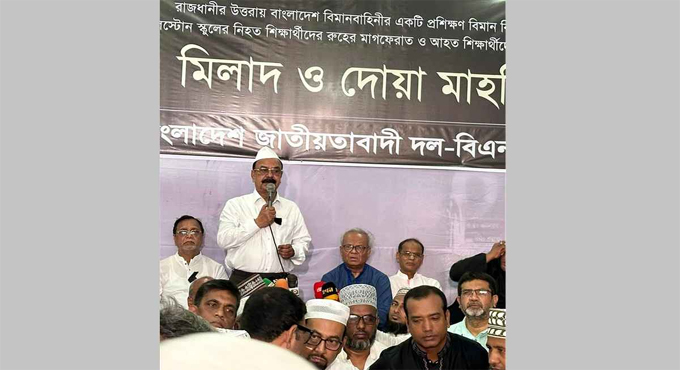রাজধানীর বিমান বন্দর থেকে বনানী-মহাখালী-মগবাজার হয়ে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে চলে যাবে কুতুবখালীর ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক পর্যন্ত। মধ্যে র্যাম্প ব্যবহার করে মহাখালী, ফার্মগেটসহ বিভিন্ন এলাকায় নামার সুযোগ থাকবে। অন্যদিকে গাজীপুর থেকে বিমানবন্দর হয়ে কেরানীগঞ্জ পর্যন্ত বাস র্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) নির্মাণের কথা থাকলেও প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হচ্ছে কেবল গাজীপুর-বিমানবন্দর অংশে। বিআরটি বিমানবন্দরের যে অংশে গিয়ে অসম্পূর্ণ রাখা হচ্ছে, সেখান থেকে শুরু হয়েছে ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্প।
বিমানবন্দরে বিআরটি শেষ করা হলে ট্রাফিক বাড়বে এক্সপ্রেসওয়েতে, যেটি পিপিপিতে নির্মাণ করছে তিনটি বিদেশী কোম্পানি।
সরকারের সংশোধিত কৌশলগত পরিবহন পরিকল্পনায় (আরএসটিপি) গাজীপুর থেকে কেরানীগঞ্জ পর্যন্ত বিআরটি নির্মাণের সুপারিশ ছিল। এটিকে চিহ্নিত করা হয় বিআরটি-৩ নামে। এ বিশেষ বাস লেন ব্যবহার করে মাত্র দেড় ঘণ্টায় গাজীপুর থেকে কেরানীগঞ্জ চলে যাওয়া সম্ভব ছিল।
নকশাগত জটিলতার কারণে বিআরটির বিমানবন্দর-কেরানীগঞ্জ অংশটি বাদ পড়ে। তখন সিদ্ধান্ত হয় বাস লেনটি বিমানবন্দর থেকে মহাখালী পর্যন্ত এগিয়ে নেয়া হবে। এজন্য প্রয়োজনীয় সমীক্ষা থেকে বিনিয়োগকারীও প্রায় ঠিক করে ফেলেছিল সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়। বিমানবন্দর-মহাখালী অংশটি বাস্তবায়নে তেমন কোনো জটিলতাও নেই। বাস্তবায়ন হলে অন্তত গাজীপুর থেকে ঢাকার মহাখালী পর্যন্ত নির্বিঘ্নে আসার সুযোগ পেতেন যাত্রীরা।
গাজীপুর-বিমানবন্দর ব্যবহার করে প্রতি ঘণ্টায় প্রায় ১২ হাজার যাত্রী বিমানবন্দরে এসে নামবে। এ যাত্রীদের শহরের ভেতরে আনার জন্য গাজীপুর-বিমানবন্দর অংশটি সম্প্রসারণ করে মহাখালী পর্যন্ত এগিয়ে নেয়ার পরিকল্পনা হয়েছিল। মহাখালী থেকে চালু করার কথা ছিল দুটি ফিডার সার্ভিস। একটি ফিডার সার্ভিস যাত্রীদের নিয়ে যেত ফার্মগেটে।
আরেকটি ফিডার সার্ভিস দিয়ে গুলিস্তান পর্যন্ত যাত্রীদের পৌঁছে দেয়ার চিন্তা-ভাবনা ছিল। তবে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় সিদ্ধান্ত নিয়েছে, শুধু গাজীপুর-বিমানবন্দর অংশ বাস্তবায়নের। এ অসম্পূর্ণ বিআরটি ঢাকার যোগাযোগ অবকাঠামোর উন্নয়নে তেমন কোনো ভূমিকাই রাখবে না বলে মনে করছেন পরিবহন বিশেষজ্ঞরা।
সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের জানান, বিমানবন্দর-গাজীপুর অংশে বিআরটি প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করতে গিয়ে অসহনীয় যানজট হচ্ছে। এ অবস্থা ঢাকার ভেতরে হতে দেয়া ঠিক হবে না। তাই বিআরটির কাজ গাজীপুর বিমানবন্দরের মধ্যেই রাখার নির্দেশনা দেন তিনি।
বিআরটি ও এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে দুটি ভিন্নধর্মী যোগাযোগ অবকাঠামো। বিআরটিতে সাধারণ সড়কে বাসের জন্য পৃথক লেন করে দেয়া হয়। যেখানে কেবল অনুমোদিত যানবাহন (সাধারণত বাস) চলতে পারে।
আরও পড়ুন : দখল হয়ে গেছে সাইকেলের লেন: ক্ষুদ্ধ ডিএনসিসির মেয়র
অন্যদিকে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রায় সব ধরনের মোটরযানের জন্য উন্মুক্ত থাকে। ফলে বিআরটি থেকে সরাসরি কোনো গাড়ি এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েতে ওঠার সুযোগ বলতে গেলে নেই। কিন্তু বিমানবন্দর যদি বিআরটির শেষ স্টেশন হয়, তাহলে সেখানে বিপুলসংখ্যক যাত্রী নামবেন, যাদের গন্তব্য হবে ঢাকার বিভিন্ন প্রান্ত।
বলা হচ্ছে প্রায় প্রতি ঘণ্টায় প্রায় ১২ হাজার যাত্রী নামবেন বিমানবন্দর স্টেশনে। এসব যাত্রী ঢাকার বিভিন্ন প্রান্তে যেতে যেসব যানবাহন ব্যবহার করবেন, সেগুলোর একটা বড় অংশ টোল দিয়ে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েতে উঠবে। ফলে বিনিয়োগকারীদের আয় বাড়বে।
ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ হচ্ছে পিপিপিতে। থাইল্যান্ড-ভিত্তিক ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান ইতালিয়ান-থাই ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড, চীনের শ্যাংডং ইন্টারন্যাশনাল ও সিনো-হাইড্রো করপোরেশন যৌথভাবে প্রকল্পটিতে বিনিয়োগ করছে। নির্মাণ ব্যয় ৮ হাজার ৯৪০ কোটি টাকা। নির্মাণ পরবর্তী ২৫ বছর টোল আদায়ের মাধ্যমে মুনাফাসহ বিনিয়োগ করা অর্থ তুলে নেবে প্রতিষ্ঠান তিনটি।
ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে ও বিআরটির গতিপথ বা রুট অ্যালাইনমেন্ট কাছাকাছি। এমন অবস্থায় বিআরটি নাকি এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে— কোন প্রকল্প ঢাকার গণপরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়নে বেশি কাজে লাগবে, জানতে চাইলে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) অধ্যাপক ড. সামছুল হক বলেন, এ রুটটিতে বিআরটির চেয়ে ভালো বিকল্প আর হতো না। বিআরটি হলো গণপরিবহন চলাচলের রাস্তা।
যেখানে নিরবচ্ছিন্নভাবে বাস চলাচলের সুযোগ পাবে। দ্রুততম সময়ের মধ্যে বিপুলসংখ্যক মানুষ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে চলে যেতে পারবে। বিপরীতে এক্সপ্রেসওয়েটির মূল ব্যবহারকারী হবে মূলত ব্যক্তিগত বাহন। এক্সপ্রেসওয়ের ওপর তো আর যাত্রী পাওয়া যাবে না। তাহলে সেখানে বাস কেন চলতে চাইবে। কিন্তু আমরা সহজ রাস্তা ছেড়ে জটিল রাস্তার দিকে এগোচ্ছি। বিআরটির বদলে এক্সপ্রেসওয়েকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি।
গাজীপুর-বিমানবন্দর বিআরটিকে করিডোর ভিত্তিক উন্নয়ন অভিহিত করে তিনি বলেন, এর মাধ্যমে কেবল বিমানবন্দর-গাজীপুর করিডোরের উন্নয়ন হবে। সামগ্রিকভাবে ঢাকার যোগাযোগ অবকাঠামোর উন্নয়নে কিংবা যে উদ্দেশ্য নিয়ে এটি নির্মাণ করা হচ্ছে, তা কোনোভাবেই সফল হবে না বলে মনে করেন এ পরিবহন বিশেষজ্ঞ।
প্রসঙ্গত, ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের মূল সড়কের দৈর্ঘ্য হবে ১৯ দশমিক ৭৩ কিলোমিটার। এক্সপ্রেসওয়ের নকশায় মোট ৩১টি র্যাম্পের সংস্থান রাখা আছে, যেগুলোর দৈর্ঘ্য আরো ২৭ কিলোমিটার। সরকারের সংশোধিত কৌশলগত পরিবহন পরিকল্পনার (আরএসটিপি) তথ্য অনুযায়ী, বাস্তবায়নের পর এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে দিয়ে প্রতিদিন প্রায় ৮০ হাজার যানবাহন চলাচল করতে পারবে। পুরো এক্সপ্রেসওয়েতে থাকবে ১১টি টোলপ্লাজা, এর মধ্যে পাঁচটি হবে এক্সপ্রেসওয়ের ওপরে।
প্রকল্পটি ২০১০-১৩ মেয়াদে বাস্তবায়ন হওয়ার কথা ছিল। যদিও এর কাজই শুরু হয়েছিল ২০১৫ সালে। তিন ধাপে বাস্তবায়নাধীন ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্পের প্রথম ধাপে বিমানবন্দর-বনানী, দ্বিতীয় ধাপে বনানী-তেজগাঁও ও তৃতীয় ধাপে মগবাজার-কুতুবখালী অংশের কাজ হবে।
এর মধ্যে প্রথম অংশ বিমানবন্দর-বনানী চালু হবে আগামী বছরের ডিসেম্বরে। এরপর চালু করা হবে বনানী-তেজগাঁও রেলগেট পর্যন্ত এক্সপ্রেসওয়ের দ্বিতীয় অংশ। আর পুরো এক্সপ্রেসওয়ের কাজ শেষ হবে ২০২৩ সালের জুনের মধ্যে।


 নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক