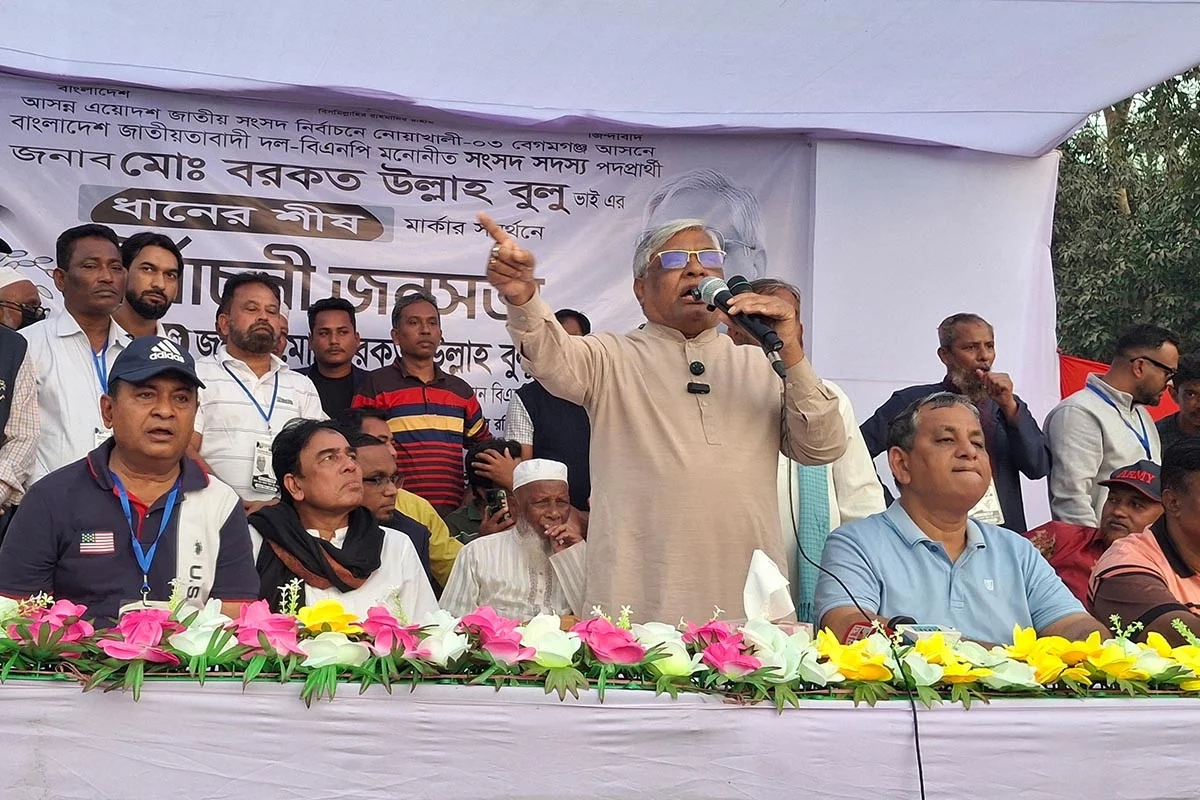কাজী সাইফুন নেওয়াজ বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)-এর দুর্ঘটনা গবেষণা ইনস্টিটিউটের সহকারী অধ্যাপক। রাজধানী ঢাকার যানজট, নগর পরিবহন ব্যবস্থা ও গণপরিবহন সমস্যাসহ প্রাসঙ্গিক বিষয়ে তিনি কথা বলেছেন।
প্রশ্ন : রাজধানী ঢাকা পৃথিবীর শীর্ষ যানজটের মহানগর হিসেবে ইতিমধ্যেই তকমা পেয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে একাধিক আন্তর্জাতিক জরিপে এই তথ্য উঠে এসেছে। করোনা মহামারী পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হওয়ার পর চলতি সপ্তাহের কয়েকদিনে আবারও অসহনীয় যানজটে নাকাল হয়েছে ঢাকাবাসী। যানজটের এই চলমান সংকটকে কীভাবে দেখছেন?
সাইফুন নেওয়াজ : পৃথিবীর অনেক দেশেই একটা সময় যানজট ছিল। ৪০/৫০ বছর আগে বিশেষ করে, ইউরোপ আমেরিকায় ব্যক্তিগত গাড়ির সংখ্যা ছিল বেশি। তারাই ব্যক্তিগত গাড়ি আবিষ্কার করেছিল। যখন তারা দেখল ব্যক্তিগত গাড়িতে যানজট বেশি হয় এবং রাস্তা দখল করে ফেলে বেশি তখন তারা বেশ কিছু পদক্ষেপ নেয়। তারা পলিসি নেয়। বিকল্প ব্যবস্থা যাতে কিনা মানুষ ব্যক্তিগত গাড়ি থেকে দূরে সরে আসে। আবার তারা এরমধ্যে রাস্তাঘাট তৈরি করছিল পরিকল্পিতভাবে। রাস্তায় দেখা গেল যে প্রতি ঘণ্টায় অল্পসংখ্যক গাড়ি চলছে কিন্তু রাস্তা তারা অনেক প্রসারিত করেছে। ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে এই কাজগুলো করেছে, কারণ রাস্তা বাড়ানো তো সহজ বিষয় নয়। আমাদের ঢাকা শহরের রাস্তাটা সেভাবে পরিকল্পনা করা হয়নি। তা যদি আমাদের পুরান ঢাকার কথা চিন্তা করি তাহলে বুঝতে পারব। বিশ্বের অন্যান্য দেশের পুরনো শহরগুলোতে অনেক বড় বড় রাস্তা। আর ঢাকায় অনেক অনেক ছোট অলিগলি রাস্তা। যখন এই রাস্তাগুলো তৈরি করে তাদের মাথায় ছিল ঘোড়ার গাড়ি যদি চলতে পারে সেই অনুযায়ী রাস্তা তৈরি করা। ঢাকা শহরের পরিধি বাড়বে মানুষ বাড়বে সে কথা তারা চিন্তা করেনি। ফলে পুরান ঢাকার রাস্তার দুই পাশে ঘরবাড়ি। পুরনো আমলের সেই ভুল বর্তমান সময়ে আমরাও করছি। রাস্তাগুলো হয়ে যাওয়ার পরে তার পাশে সুউচ্চ বিল্ডিংগুলো আমরাও করছি এখনো। আমাদের চিন্তাগুলো ঘোড়ার আমলে যেমন ছিল বর্তমান প্রাইভেটকারের আমলেও একই রয়েছে। সম্প্রতি পূর্বাচল নতুন কিছু সিটি হচ্ছে, সেখানে চেষ্টা করা হচ্ছে। ইন্টারসেকশনগুলো বড় করা হচ্ছে। তবে সামগ্রিকভাবে চিন্তাগুলো না করাতে ঢাকা শহরটা অপরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠছে।
প্রশ্ন : রাজধানী ঢাকার আয়তন ও জনসংখ্যার তুলনায় এখানে সড়কের যে দৈর্ঘ্য বা অনুপাত এটা কি যানজটের একটা বড় কারণ বলে মনে করেন?
সাইফুন নেওয়াজ : আসলে সড়কের ক্ষেত্রে ভূমি ব্যবস্থাপনা একটা বড় বিষয়। ঢাকা শহরই না, বাংলাদেশের কোনো সড়কের পাশেই এই পরিকল্পনা নেওয়া হয় না। সড়কটা যখন হবে ভূমি ব্যবস্থাপনা কীভাবে মানে তখন তার পাশে দোকানপাট কী হবে, অন্যান্য স্থাপনা কত দূরে হবে তার কোনো পরিকল্পনা নেই। বিল্ডিংগুলো অপরিকল্পিতভাবে হয়ে গেছে। ফলে আমরা চাইলেও এখন আর রাস্তা বাড়াতে পারছি না। রাস্তা বাড়াতে হলে এখন যে পরিমাণে বিল্ডিং ভাঙতে হবে ঢাকা শহরে সেটা অনেক কষ্টসাধ্য। বিজিএমইএ ভবন ভাঙতে গিয়ে আমরা টের পেয়েছি। আরেকটা বড় সমস্যা হলো, সবাই চেয়েছে নিজের বাসার সামনে থেকে একটা বড় রাস্তা বের হোক। ফলে প্রচুর গলি রাস্তা যুক্ত হয়েছে, এটা মানে যেই শহরগুলোকে আমরা আইকন মনে করি, সেখানে এই ইন্টারসেকশনগুলো দুই তিন কিলোমিটার দূরে দূরে। আর আমাদের গুলি একটু পরপর। এই ইন্টারসেকশনগুলো একেকটা যানজট তৈরির জোন। কারণ এখানে মানুষ এসে দাঁড়ায়, রিকশা এসে দাঁড়ায়, আবার বাস এসে দাঁড়ায় কারণ যেখানে মানুষ সেখানে বাস। আবার মানুষের জটলাকে ঘিরে দোকানপাটও তৈরি হয় ফলে এটা একটা যানজটের বড় কারণ। ১০ কিলোমিটারের একটা জার্নির জন্য দশ-বারোটা ইন্টারসেকশন থাকে তাহলে যানজট যাবে কীভাবে? ঢাকা শহরে যে পরিমাণ ইন্টারসেকশন রয়েছে সেটিও যানজটের বড় একটি কারণ বলে আমরা চিহ্নিত করেছি। সমাধানের কথা বলি, আমাদের পরিকল্পনা নিতে হবে এত যে ইন্টারসেকশন এগুলোর সব আমরা মেইন রোডের সঙ্গে রাখব।
প্রশ্ন : সাম্প্রতিক এক পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, রাজধানী ঢাকায় নিবন্ধিত ব্যক্তিগত গাড়ির সংখ্যা ৩ লাখ ১৭ হাজার ৫০৯টি। অন্যদিকে, ব্যক্তিগত গাড়ির দখলে সড়কের ৭৬ দশমিক ৩৫ শতাংশ থাকলেও এসব গাড়িতে যাত্রী পরিবহন করা হয় মোট যাত্রীর মাত্র ২৫ শতাংশের মতো। খেয়াল করার মতো বিষয় হলো রাইড শেয়ারিং চালু হওয়ার পর ঢাকায় মোটরসাইকেলের সংখ্যা বেড়েছে বিপুল হারে। ব্যক্তিগত গাড়ির এই বিপুল আধিক্যকে কীভাবে দেখেন?
সাইফুন নেওয়াজ : এদেশে ব্যক্তিগত গাড়ির সংখ্যা বিপজ্জনক হারে বাড়ছে। শহরে এখন তিন থেকে সাড়ে তিন লাখ প্রাইভেটকার রয়েছে। মোটরসাইকেলের তুলনা করলে ঢাকা শহরে যত গাড়ি আছে তার অর্ধেকই মোটরসাইকেল। তাই সব মিলিয়ে ৭০ থেকে ৭৫ শতাংশ ব্যক্তিগত গাড়ি। তো আমাদের রাস্তা সরু এবং রাস্তার পরিমাণ বাড়ানো সম্ভব নয় তাহলে কোনোভাবেই ব্যক্তিগত গাড়ি বাড়তে দেওয়া ঠিক হবে না। মোটরসাইকেল বাড়ছে দিন দিন, পরিবহন হিসেবেই আমরা মোটরসাইকেলকে ব্যবহার করছি। যে কেউ ইচ্ছে করলেই ব্যক্তিগত প্রাইভেট কার নামাচ্ছে, রাইড শেয়ারিং অ্যাপ ব্যক্তিগত গাড়ি বাড়ছে। আবার মোটরসাইকেল বাড়ার কারণে মানুষকে গণপরিবহন আকৃষ্ট করার ক্ষেত্রে অনেক বেগ পেতে হবে। রাইড শেয়ারিংয়ের গাড়িগুলো বিশৃঙ্খলা তৈরি করছে এবং যানজট হচ্ছে। মানুষের ব্যক্তিগত প্রয়োজনের জায়গা হলো কম খরচে যাতায়াত করা এবং একটি আরামদায়ক জার্নি। তাই গণপরিবহনের ব্যবস্থার প্রয়োজন। গণপরিবহনের জন্য আলাদা লেন তৈরি করে দিতে হবে।
প্রশ্ন : সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত রাজউক-এর তথ্যমতে, ঢাকার সড়কগুলোর মাত্র ১ শতাংশ দখলে রাখে যাত্রীবাহী পাবলিক বাস। অথচ এই বাসগুলোই প্রায় ৬০ শতাংশ যাত্রী পরিবহন করে। ঢাকার মতো পৃথিবীর আর কোনো বড় মহানগরে গণপরিবহনের এমন দুর্দশা আছে কি?
সাইফুন নেওয়াজ : এক্ষেত্রে পরিকল্পনা নিতে হবে। আমরা দেখি পরিবহন ব্যবস্থায় কোনো শৃঙ্খলা নেই। রাস্তায় চার মালিকের চারটি বাস যখন একসঙ্গে চলে তখন সামনে থেকে তাদের যাত্রী ওঠানোর জন্য প্রচ- প্রতিযোগিতা থাকে। সড়কে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং যানজট তৈরি হয়। এই পরিস্থিতিতে যাত্রীরাও যানবাহনে চলতে চান না। আমাদের বাস রুট রেশনালাইজেশন খুবই জরুরি। পৃথিবীর বেশিরভাগ দেশ যারা যে শহরে যানজট ছিল তারা গণপরিবহনকে রেশনালাইজেশন করে যানজটটা কমিয়েছে। এখানেও তা করতে হবে।
প্রশ্ন : ঢাকার গণপরিবহন খাতের একটি প্রধান সমস্যা মনে করা হয় এখানে সক্রিয় বাস কোম্পানিগুলোর মধ্যকার বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য। ধারণা করা হয় ঢাকায় বাস মালিকের সংখ্যা দুই হাজারেরও বেশি। আর ঢাকা ও আশপাশে ২০০-এর বেশি রুটে বাস চলাচল করে। বিভিন্ন কোম্পানির বাস একই ছাতার নিচে এনে পরিচালনা করা হলে এই সংকট কাটবে বলে মনে করেন কি?
সাইফুন নেওয়াজ : একটি ছাতার নিচে সব বাস চললে এবং রুট রেশনালাইজেশন করলে অবশ্যই যানজট অনেক কমবে। সবাইকে একই রুটের আওতায় এবং এক ছাতার নিচে আনলে একে অপরের সঙ্গে যে প্রতিযোগিতা করার বিষয়টি সেটি অবশ্যই কমবে। যানজট এবং দুর্ঘটনা কমবে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ এ পদ্ধতিতে চলে সফল হয়েছে। ঢাকায় চার থেকে পাঁচ হাজার বাস চলে আর মালিক যদি হয় ২০০০ তাহলে কারও কারও মাত্র একটি আছে। এটা কোনো সিস্টেম হতে পারে না। যানজট নিরসন করতে হলে এবং শৃঙ্খলা আনতে হলে এখানে সরকারের একটা মনিটাইজেশন এবং রেগুলারাইজেশন দরকার। এখানে মালিকদের নিয়ে সরকারের বসতে হবে। মালিকরা সবাই বসে একটা রুট ঠিক করবে তারা কতগুলো বাস চালাতে চায়, কীভাবে চলতে চায়। চালক কেমন হবে, গাড়ির কোয়ালিটি কেমন হবে, চালকের কোয়ালিটি কী হবে, বেতন কত হবে, যাত্রীদের সঙ্গে কি ধরনের ব্যবহার হবে সবই সরকারকে ঠিক করে দিতে হবে। ফিটনেস দেখতে হবে। সরকার নিয়ম ঠিক করবে এবং স্ট্যান্ডার্ড করবে আর যাদের সে ক্যাপাসিটি আছে নিয়ম পূরণের তাদের গণপরিবহন নামানোর অনুমতি দিতে হবে। আবার সরকারের দায়িত্ব হলো এই পরিবহনগুলোর পরিবেশ দেওয়া।
প্রশ্ন : ঢাকার পরিকল্পিত পাঁচটি মেট্রোলাইন ২০৩৫ সালের মধ্যে শেষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। কিন্তু গবেষকরা বলছেন তখনো ঢাকার মোট যাত্রীর ১৭ শতাংশ মেট্রো ব্যবহার করার সুযোগ পাবেন। সেক্ষেত্রে ঢাকার পাবলিক বাস সার্ভিসের সংখ্যা ও মান বৃদ্ধি এবং ব্যক্তিগত গাড়ির সংখ্যা কমিয়ে আনার চ্যালেঞ্জ কি থেকেই যাবে?
সাইফুন নেওয়াজ : যদি ব্যক্তিগত গাড়ি নিয়ন্ত্রণ করা না যায় তাহলে যানজট কমানো কখনোই সম্ভব না। এই কথা চিন্তা করতে হবে যেন মানুষ খুব সহজেই তার ঘর থেকে বেরিয়ে পরিবহন পায় এবং তার গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতে পারে। মেট্রো করলেও সে কথাটি মাথায় রাখতে হবে। যেন মেট্রো থেকে সে নামলেই তার গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য গাড়িগুলো পায়। তাই মেট্রোর সঙ্গে অন্যান্য গণপরিবহনের সমন্বিত উদ্যোগ নিতে হবে। তারপর পার্কিংয়ের ব্যবস্থা থাকতে হবে। শুধু গণপরিবহন বাড়ালেই হবে না যানজটের জন্য আমাদের যেহেতু রাস্তা বাড়ানোর সুযোগ নেই তাই অন্য পথগুলোর দিকে মনোযোগ দিতে হবে। খালের কানেকটিভিটি কীভাবে তৈরি করা যায় তা ঠিক করতে হবে। রামপুরা ধানমন্ডির দিকে যে লেকগুলো রয়েছে সেগুলো যদি আমরা ব্যবহার করতে পারি নৌপথ হিসেবে এবং সেগুলো ট্রেনের সিডিউলের সঙ্গে সমন্বয় করে মানুষের যে সময় প্রয়োজন সেই সময় যদি আমরা এই ট্রেনের টাইমটা দিতে পারি তাহলে অনেকটাই সহজ। পাশাপাশি পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে যারা ঢাকায় আসবে তাদের অফিস শিডিউলের সঙ্গে ট্রেনের সিডিউলগুলো তৈরি করতে হবে। একটা সময় সদরঘাট থেকে গাবতলী পর্যন্ত নৌরুট ছিল। ইচ্ছাকৃতভাবে এটাকে নষ্ট করলাম। ক্যানেল প্রজেক্টগুলোকে অ্যাকটিভ করতে হবে।


 নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক